যেভাবে হয়েছিল প্রানের উতপত্তি
যেভাবে হয়েছিল প্রানের উতপত্তিঃ
প্রানের উৎপত্তি নিয়ে বিশ্লেষণমুলক লেখা
প্রানের উৎপত্তি নিয়ে ধর্মীয় সৃষ্টিবাদ ও বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ পরস্পর বিপরীত অবস্থানে আছে এবং অধিক বিতর্কের ঝড় তুলেছে । সৃষ্টিবাদের মাধ্যমে জীব এবং ইউনিভার্স সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তা গল্প বা মিথের মত মনে হয় এবং এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাওয়া যায় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে। পক্ষান্তরে বিবর্তনবাদ বলে এক থেকে রূপান্তর হয়ে বহুর উৎপত্তি হয়েছে । এটি বিজ্ঞানীদের স্বীকৃত মতবাদ ।
সাধারণভাবে প্রশ্ন জাগে প্রাণ কি এবং কিভাবে প্রাণের বিবর্তন হল ?
প্রাণ সৃষ্টির উৎস অনুসন্ধানের পূর্বে পদার্থ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণার প্রয়োজন আছে । আমরা জানি পদার্থ দুই প্রকার । মৌলিক ও যৌগিক । যে সব পদার্থের সমন্বয়ে উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয় তাকে বলে জৈব পদার্থ এবং বাদবাকিগুলো অজৈব পদার্থ । জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, জৈব পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর কেন্দ্রে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু থাকে, যাকে কার্বন বলা হয় । কার্বনের বাংলা অঙ্গার বা ছাই । জৈব পদার্থ পুড়ালে সবসময় এই অঙ্গার পাওয়া যাবে ।
তাহলে বুঝা গেল কার্বনই জৈব পদার্থের মূল উপাদান । কিন্তু এটি শেষকথা নয় । পদার্থবিশেষে এর সাথে মিশে থাকে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, গন্ধক এবং আরও অনেক পদার্থ । জৈব পদার্থের অণুর গর্ভস্থ কার্বনের সাথে এইসব পদার্থের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মিলনের ফলে জন্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন জৈব পদার্থের । যেমন-কার্বন ও হাইড্রোজেন মিশালে পাওয়া যায় হাইড্রোকার্বন ।
জীবদেহ যেহেতু জৈব পদার্থ, এর ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের । খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হল কার্বন সংগ্রহ করা । জীব-জন্তু কার্বন সংগ্রহ করে লতা-পাতা, তরি-তরকারি, কীট-পতঙ্গ, মাছ-মাংস ইত্যাদি থেকে । সংগৃহীত কার্বন বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে রূপান্তরিত হয় জৈব পদার্থে । উদ্ভিদ কার্বন সংগ্রহ করে বাতাস থেকে । এখন প্রশ্ন জাগতে পারে এই জৈব পদার্থ সৃষ্টি হল কিভাবে ?
আকাশে আমরা যেসব নক্ষত্র দেখে থাকি তাদের মধ্যে আয়তন ও উত্তাপের পার্থক্য আছে । সর্বনিম্ন ৪০০০˚ সে. থেকে সর্বোচ্চ ২৮০০০˚ সে. উত্তাপের নক্ষত্র আছে । স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রদের কার্বন পরমাণুরা একা একা ভেসে বেড়ায় । এরা অন্যকোন পরমানুর সাথে জোড় বাঁধে না । কিন্তু যে সব নক্ষত্রের উত্তাপ ১২০০০˚ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে মিলে সৃষ্টি করেছে হাইড্রোকার্বন । এই হাইড্রোকার্বন একটি জৈবিক পদার্থ । বিজ্ঞান বলে এখান থেকেই জৈবিক পদার্থ সৃষ্টির সূত্রপাত । এ তো গেল নক্ষত্রের কথা, পৃথিবীতে কার্বন সৃষ্টি হল কিভাবে ?
আমরা জানি সূর্যের বাইরের উত্তাপ প্রায় ৬০০০˚ সে. । সূর্যের মধ্যে দেখা গেছে একাধিক মৌলিক পদার্থের মিলন ঘটতে । সেখানে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেন, কার্বনের সঙ্গে কার্বনের মিলন ঘটছে । ফলে সেখানে একাধিক জৈব পদার্থের জন্ম হয়েছে । উল্কাপিন্ডের দেহ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, উল্কার দেহে কার্বন ও ধাতুর মিলনে জন্ম হয়েছে কার্বাইড । ইহাও একটি জৈব পদার্থ ।
সূর্য, নক্ষত্র ও উল্কার দেহে যে প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ জন্মেছে, পৃথিবীতেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে । পৃথিবীতে বর্তমানে যে পরিবেশ বিরাজমান আদিতে তেমনটি ছিল না । পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের খন্ডিত টুকরো । জন্মলগ্নে এই গ্রহগুলো ছিল জলন্ত এবং তাপমাত্রা প্রায় সূর্যের সমান । তখন এগুলো গ্রহ ছিল না, নক্ষত্রই ছিল । কোটি কোটি বছর জ্বলার পর এগুলোর জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলে এগুলো গ্রহে পরিণত হয় । সূর্য থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে আকর্ষণ করে প্রদক্ষিণ করছে । উপগ্রহগুলো গ্রহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই এগুলো গ্রহকেই আকর্ষণ করে প্রদক্ষিণ করছে । যেমন-চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ । এটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি অংশ, তাই চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে ঘুরছে । আদি পৃথিবীর জলন্ত সময়কালেই পৃথিবীতে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে ।
প্রোটিন তৈরি হয় হাজার হাজার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে । বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটিন তৈরি হওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ বজায় ছিল । লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তরে তৈরি হয়েছিল প্রোটিন । এই প্রোটিন হতে জন্ম নিয়েছিল জীবদেহের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম ।
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে প্রকৃতির কাজ কি ? প্রকৃতির একমাত্র কাজ পরিবর্তন করা । এই পরিবর্তনকেই বিবর্তন বলা হয় । যা আমাদের চোখের গোচরে ঘটছে কিন্তু আমরা সেভাবে চিন্তা করছি না । তবে পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তুর বিবর্তনের সময়-কাল এক নয় । এদের মধ্যে ব্যবধান অনেক দীর্ঘ । বিবর্তনের জন্য যেটা জরুরী তা হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ । আমরা জানি পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে পানি জমে বরফে পরিণত হয় । বরফ পানির বিবর্তিত রূপ । কিন্তু বাংলাদেশের পানিকে প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরফে রূপান্তরিত করতে পারে না । এটার কারণ হচ্ছে পরিবেশের তারতম্য । প্রকৃতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুধকে দধিতে ও তালের রসকে তাড়িতে পরিবর্তন করতে পারে । কিন্তু রেডিয়ামকে শীশায় পরিণত করতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বছর । ঠিক অনুরূপ কার্বন (জৈব পদার্থ) হতে একটি প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে প্রায় একশত কোটি বছর । পদার্থ জৈব হলেই তা জীব একথা বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ না পায় । কোন পদার্থে দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি এই লক্ষণ দুটি যদি প্রকাশ পায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঐ পদার্থটি সজীব । প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য উপাদান প্রোটিন এবং ইহা ছাড়াও আরও বিভিন্ন জৈব-অজৈব পদার্থ । ইহা আদিম সমুদ্রের জলে গোলা দ্রব অবস্থায় ছিল । ইহা সম্পূর্ণ জলে মিশে না, জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে । যার ইংরেজি নাম কলয়ডাল সলিউশন । এই সলিউশন জৈব বা অজৈব উভয় পদার্থের হতে পারে । অজৈব পদার্থের সলিউশন দ্রবীভূত হয়ে জলের নিচে পড়ে থাকে । এখানে জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে একটি চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে । জৈব পদার্থের সলিউশন জলে ভেসে থাকার সক্ষমতা অর্জন করেছে, পক্ষান্তরে অজৈব পদার্থের সলিউশন জলে আত্মসমর্পণ করেছে । জৈব কলয়ডাল সলিউশনের মধ্যে এই স্বকীয়তা দেখা গেছে যে, সে জলের শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজী নয় ।
কলয়ডাল সলিউশনের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ দেখা যায় । এটি জলে ভাসমান অন্য জৈব-অজৈব পদার্থকে আত্মসাৎ করে নিজ দেহ পুষ্ট করতে থাকে । এই প্রক্রিয়া লক্ষ লক্ষ বছর চলতে থাকলে কলয়ডাল জৈব পদার্থটি আয়তন ও ওজনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটা পর্যায়ে এসে ফেটে দুই টুকরা হয়ে যায় । এই টুকরাদ্বয় পূর্বের মত আলাদা আলাদাভাবে পুষ্ট হতে থাকে এবং আরও একটা পর্যায়ে এসে ফেটে চার টুকরা হয় । কালের পরিক্রমায় চার টুকরা ফেটে হয় আট টুকরা । এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল কলয়ডাল পদার্থটির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির ধারাটি । আমরা জানি জীবনের প্রধান বৈশিষ্টের মধ্যে অন্যতম হল পুষ্টি ও বংশবিস্তার করা । এই বিশেষ ধরনের কলয়ডাল পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজম বা সেল । বাংলায় জীবকোষ বলা হয় । আদিম সমুদ্রের জলে অতি সামান্য প্রোটোপ্লাজম বিন্দুকে আশ্রয় করেই প্রথম প্রাণের অভ্যুদয় এবং পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল জীবনের অভিযান । এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোন দ্বিমত নেই ।
বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন ‘প্রাণ’ শক্তিটি কোন কোন পদার্থের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি অভিনব শক্তি । পৃথিবীর আদি অবস্থায় তাপ, আলো, বায়ুচাপ, জলবায়ুর উপাদান ইত্যাদির পরিমাণ প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল ছিল বলে তখন প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল । প্রকৃতির সেই আদিম অবস্থা আর নেই, তাই এখন চলছে বীজোৎপন্ন প্রাণ প্রবাহ বা প্রাণ থেকে প্রাণ উদ্ভবের ধারা । কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছিলেন কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা যায় কি না ? ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেড্রিক ওহলার টেস্টটিউবে ইউরিয়া (জৈব পদার্থ) তৈরি করে প্রমাণ করেন, প্রকৃতির (ঈশ্বর) ন্যায় মানুষ জৈব পদার্থ তৈরি করতে পারে । এরপর ১৯৬৭-৬৮ সালের শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আর্থার কোর্ণবার্গ এবং তাঁর সহকারীগণ মিলে টেস্টটিউবে অজৈব পদার্থ C. H. O. N. ইত্যাদির সংমিশ্রণে জৈব ভাইরাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন । উক্ত ভাইরাস প্রকৃতজাত (ঈশ্বরসৃষ্ট) ভাইরাসের মত নড়াচড়া করে ।
এবার দেখা যাক প্রাণের বিবর্তন কিভাবে হয়েছিল । প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষের দিক পর্যন্ত জীবকোষগুলোর ইন্দিয়, চেহারা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়নি । সর্বশরীর দিয়ে চুষে এরা আহার করে । পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পেলে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে । আঘাত পেলে সর্বশরীরে শিহরণ উঠে । এতে দেখা যায় এসব জীবকোষে জীবনের আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে বোধশক্তি । বর্তমানে খাল-বিলের নোংরা জলে তুলতুলে জেলির মত শেওলা জাতীয় এক প্রকার জলীয় পদার্থ দেখা যায় । অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এদের শরীরে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু জীবকোষ । এদের বলা হয় অ্যামিবা । এরা এককোষ বিশিষ্ট জীবজগতের আদিম প্রাণী ।
ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে এক প্রকার পরিবর্তন আসে তা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করা যায় । তেমনি কালের পরিক্রমায় কোন কোন আদিম জীবকোষের স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসে । এরা একা একা না থেকে মৌমাছির মত জটলা বেঁধে থাকতে আরম্ভ করে । জটলার বাইরের কোষগুলো খাদ্য সংগ্রহ করলে, তা ভেতরের কোষগুলো চুষে নেয় এবং স্বস্থানে থেকে এদের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হতে থাকে । এর ফলে জটলাটির আকৃতি বৃদ্ধি পায় । জটলার ভিতরের কোষগুলোর স্বতন্ত্র সত্ত্বা বজায় থাকলেও বাইরের দিকের কোষগুলোর অবস্থা হয়ে পড়ে ভিন্ন । এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির জটলা তৈরি হয়ে সমুদ্রজলে বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে ।
আজ থেকে একশত কোটি বছর পূর্বে ভূপৃষ্টের কোথাও উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল না । সমুদ্রের জল কিছুটা গরম, লবণহীন এবং এতে মিশে আছে নানা প্রকার জৈব-অজৈব পদার্থ । কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল অত্যাধিক । আকাশের সমস্ত জলীয় বাস্প বৃষ্টি আকারে পতিত না হওয়াতে আকাশ ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা । এ অবস্থায় ভূপৃষ্টের কোথাও সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না । বাতাসে আছে স্বল্পমাত্রার অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অধিক । এই পরিবেশে সমুদ্রের জলে জীবাণুদের বংশবিস্তার চলছিল ধীরে ধীরে । কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল হলে এবং আকাশের সব জলীয় বাষ্প ঝরে পড়লে, ভূপৃষ্টে অবাধে নেমে আসে সূর্যালোক । এই সূর্যালোক পেয়ে সমুদ্রজলে জীবাণুদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয় ।
শীতের দিনে রৌদ্র সবার প্রিয় । কিন্তু সবাই রোদ পোহাবার সুযোগ পায় না । আবার রোদ পোহালে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়না, যদি হত সবাই রোদই পোহাত । সমুদ্রজলে যেসব জীবাণু রোদ পোহাবার সুযোগ পেল, তারা এক আশ্চর্য সুবিধাও পেয়ে গেল । তারা দেখল রোদ পোহালে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় । এতে ঐসব জীবাণু একস্থানে স্থির থেকে রোদ পোহাইয়া দেহ পুষ্ট ও বংশবৃদ্ধি করতে লাগল । এরূপ সুবিধাভোগী জীবাণুরা কালক্রমে উদ্ভিদে পরিণত হল । আর যে সব জীবাণুরা জলের গভীরে থাকার দরুন সূর্যালোকের স্পর্শ পেল না, তাদের খাবার সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি না করে উপায় থাকল না । এইসব অসুবিধাভোগী জীবাণুরা হল জীব বা জন্তু ।

গাছের পাতায় সূর্যালোক পতিত হলে এক প্রকার সবুজ রঙের প্রলেপ পড়ে । একে বলা হয় ক্লোরোফিল । পাতার গায়ে বাতাস লাগলে ক্লোরোফিল বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করে একে কার্বন ও অক্সিজেন এই দুইভাগে বিভক্ত করে । কার্বনকে গাছের দেহপুষ্টির জন্য রেখে অক্সিজেন বাতাসে ফিরিয়ে দেয় । ঠিক তেমনি সমুদ্রজলে যেসব জীবাণুদের শরীরে সূর্যালোক পড়েছিল, তাদের দেহে জমেছিল ক্লোরোফিল । ফলে এর সাহায্যে জীবাণুরা খাদ্য সংগ্রহ করে অচল জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল । এরাই জাতিতে উদ্ভিদে পরিণত হল । আগেই বলেছি সে সময়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল অত্যাধিক । ফলে এসব উদ্ভিদাণুরা সহজে অতি মাত্রা পুষ্টিকর খাদ্য কার্বন পেয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে । বিবর্তনের ধারা অনুসারে এরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করে । বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় শেওলা জাতীয় নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ ।
সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত জীবাণুরা অন্য উপায়ে কার্বন সংগ্রহের চেষ্টায় থাকল । তারা উদ্ভিদাণুর দেহে প্রচুর কার্বন মজুত পেয়ে এদের খাওয়া শুরু করল । হাতের নাগালের খাবার শেষ হয়ে আসলে খাবার সংগ্রহের তাগিদেই তারা চলাফেরায় অভ্যস্ত হল । উদ্ভিদাণূদের খেয়ে খেয়ে জীবাণুদের রাক্ষুসেপনা বেড়ে গেল । এতে সবল জীবাণুরা দুর্বল জীবাণুদের খেতে আরম্ভ করল । ফলে আত্মরক্ষার্থে দুর্বল জীবাণুরা পালাতে লাগল এবং সবল জীবাণুরা তাদের আক্রমণ করার জন্য তাড়া করতে লাগল । এতে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দ্রুত চলাচলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল । এভাবে বিবর্তনের ধারা মতে তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল । এই বীজাণুদের বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপে দেখা যায় ট্রাইলোবাইট নামক কয়েক শ্রেণীর পোকা জাতীয় জলজ জীব।

প্রকৃতির রীতিই হল পরিবর্তন করা । প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জীবজগতে যে রূপান্তর ঘটে থাকে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বিবর্তন (Evolution) বলে । বিবর্তন দুই প্রকার । যথা-কৃত্রিম নির্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন । কৃত্রিম নির্বাচন সময়সাপেক্ষ নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রাণীর সামান্য পরিবর্তন হতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বছর । পৃথিবী জন্মের পর প্রায় ২০০ কোটি বছর লেগেছে জীবসৃষ্টির অনুকূল তাপের সৃষ্টি হতে । এরপর প্রায় ১৫০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হয়েছে । মাত্র ৫০ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে চোখে দেখার মাধ্যমে চিনতে পারার মত প্রাণী । কিন্তু ৫ হাজার বছর পূর্বের কোন লিখিত ইতিহাস মানুষের হাতে নেই । তাহলে বিজ্ঞানীরা এতসব জেনেছেন কিভাবে ? বিজ্ঞানীরা বলেন সৃষ্টির ইতিহাস লিখা আছে সৃষ্টি পদার্থের গর্ভে । তারা জীবের অতীত ইতিহাস জেনেছেন জীবাশ্ম বা ফসিল পরীক্ষা করে ।
ভূবিজ্ঞানীরা মাটির বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে জানতে পারেন কোন স্তরের বয়স কত । কোন জীব-জন্তুর দেহ বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকলে এর কঙ্কাল পাথরের আকার ধারণ করে । বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় জিবাশ্ম বা ফসিল । ভূগর্ভস্থ কোন বিশেষ স্তর থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত ফসিল পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, ঐ জন্তুটি কোন যুগে বা কত বছর পূর্বে জীবিত ছিল এবং এর আকৃতি, প্রকৃতি, চাল-চলন, খাদ্যাভাস কি রকম ছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো ।


ডারউইনের বিবর্তনবাদ একটি হাইপোথিসিস । তিনি প্রকৃতির আচরণ ধরতে পেরেছিলেন । কিন্তু বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় ফসিলের মধ্যে । আর এই ফসিলের সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের নিবিঢ় সম্পর্ক । তাই বিবর্তন বুঝতে হলে যুগ সম্পর্কেও কিছুটা ধারণার প্রয়োজন আছে ।
ডারউইনের বিবর্তনবাদ একটি হাইপোথিসিস । তিনি প্রকৃতির আচরণ ধরতে পেরেছিলেন । কিন্তু বিবর্তনের সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় ফসিলের মধ্যে । আর এই ফসিলের সাথে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের নিবিঢ় সম্পর্ক । তাই বিবর্তন বুঝতে হলে যুগ সম্পর্কেও কিছুটা ধারণার প্রয়োজন আছে ।
ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরকে বিজ্ঞানীরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন । প্রত্যেক ভাগকে বলা হয় একটি যুগ । আজ থেকে ৫০ কোটি বছর পূর্বের সমস্ত যুগকে একত্রে বলে প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগ । এটিকে আর্কেও জোইক বা মহাযুগও বলা হয় । এই যুগে যেসব প্রাণী বর্তমান ছিল তার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র । তাদের দেহ নরম তুলতুলে ছিল বিধায় ভূগর্ভে কোন ফসিল পাওয়া যায় না । তাই তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই । ক্যামব্রিয়ান যুগ শুরুর পর থেকে কোন কোন প্রাণীর দেহ কঠিন খোলস দ্বারা আবৃত হয় । চিংড়ি, কাঁকড়া এই যুগের প্রাণী । এই যুগ থেকেই শিলালিপি বা ফসিল পাওয়া যায় এবং এর সাহায্যে ইতিহাস জানা যায় বলে বিজ্ঞানীরা এই যুগকে বলেন ঐতিহাসিক যুগ ।
ঐতিহাসিক যুগের তিনটি ভাগ আছে । যথা- ১. পুরাজীবীয় ২. মধ্যজীবীয় ও ৩. নবজীবীয় যুগ । এই তিনটি যুগের ব্যাপ্তিকাল ৫০ কোটি বছর । পুরাজীবীয় যুগটি শুরু হয়েছিল ৫০কোটি বছর আগে । এর ব্যাপ্তিকাল ছিল ৩১ কোটি বছর এবং ১৯ কোটি বছর পূর্বে এর সমাপ্তি ঘটে । এই যুগটির ৬টি উপযুগ আছে । মধ্যজীবীয় যুগটির ব্যাপ্তিকাল ১২ কোটি বছর । এটি ১৯ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ৭ কোটি বছর পূর্বে । এর উপযুগ আছে ৩টি । নবজীবীয় যুগটি হচ্ছে বর্তমান যুগ । এটি ৭ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে । এর আছে ৫টি উপযুগ । সর্বশেষ উপযুগটির নাম প্লিসটোসেন উপযুগ । এই উপযুগটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে শুরু হয়ে এখনও চলছে । জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উপযুগটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ ।
ঐতিহাসিক যুগের তিনটি ভাগ আছে । যথা- ১. পুরাজীবীয় ২. মধ্যজীবীয় ও ৩. নবজীবীয় যুগ । এই তিনটি যুগের ব্যাপ্তিকাল ৫০ কোটি বছর । পুরাজীবীয় যুগটি শুরু হয়েছিল ৫০কোটি বছর আগে । এর ব্যাপ্তিকাল ছিল ৩১ কোটি বছর এবং ১৯ কোটি বছর পূর্বে এর সমাপ্তি ঘটে । এই যুগটির ৬টি উপযুগ আছে । মধ্যজীবীয় যুগটির ব্যাপ্তিকাল ১২ কোটি বছর । এটি ১৯ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ৭ কোটি বছর পূর্বে । এর উপযুগ আছে ৩টি । নবজীবীয় যুগটি হচ্ছে বর্তমান যুগ । এটি ৭ কোটি বছর পূর্বে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত চলছে । এর আছে ৫টি উপযুগ । সর্বশেষ উপযুগটির নাম প্লিসটোসেন উপযুগ । এই উপযুগটি ৫০ লক্ষ বছর পূর্বে শুরু হয়ে এখনও চলছে । জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উপযুগটি অসীম গুরুত্বপূর্ণ ।
পুরাজীবীয় যুগে ভূপৃষ্টে কোন জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নি । তবে সমুদ্রে জলজ উদ্ভিদ ও ট্রাইলোবাইট নামক আলপিনের মাথার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র এক জাতীয় পোকার সন্ধান পাওয়া যায় । কয়েক কোটি বছর পর এই পোকার আকৃতি হয়েছে প্রায় এক ফুট । এদের সব শাখার বিলুপ্তি ঘটলেও বর্তমানে দুই একটি শাখা বেঁচে আছে । গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া হচ্ছে তাদেরই বংশধর । ট্রাইলোবাইট প্রাণীদের একটি দল নদী বা হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল । ভূ-কম্পের ফলে নদী বা হ্রদ শুকিয়ে গেলে এদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়, কিছু সমুদ্রে চলে যায় এবং কোন কোন দল স্থলেও বেঁচে থাকে । স্থলে বেঁচে যাওয়া দলেরই বিবর্তিত রূপ হচ্ছে মাকড়সা, বৃশ্চিক ইত্যাদি । এদের মধ্যে কোন কোনটি উড়বার ক্ষমতা লাভ করে হয় পতঙ্গ । যে দলটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিল কয়েক কোটি বছরের মধ্যে তাদের দেহ চর্ম বা খোলসে আবৃত হয় ।
কাঁকড়া, কাছিম, শামুকের মত বর্মধারী জীবেরা যত সহজে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পরে, চর্মধারী জীবেরা তত সহজে পারে না । আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দ্রুত চলাচলের জন্য চর্মধারী জীবের দেহে তৈরি হয় মেরুদন্ড । আজ থেকে প্রায় ৩৫ কোটি বছর পূর্বে অর্ডোভিসিয়ান উপযুগের (পুরাজীবীয় যুগ) শেষের দিকে প্রথম মেরুদন্ড বিশিষ্ট যে সব জীবের জন্ম হয়, তাদের একটি দল হচ্ছে মাছ । মাছ সাধারণত কানকোর সাহায্যে জল হতে বাতাস সংগ্রহ করে শ্বাসকার্য চালায় । দেখা যায় কোন কোন মাছের ফুসফুস গঠিত হয়েছিল। আফ্রিকার সমুদ্রে এ জাতীয় মাছে অস্তিত্ব আছে । ফুসফুসওয়ালা মাছ জলে ও স্থলে বেঁচে থাকতে পারে । উপকূলের কাছাকাছি বসবাস রত মাছেরা অনেক সময় জোয়ার ও ঢেউয়ের আঘাতে ডাংগায় উঠে পড়ে । এদের কিছু কিছু মারা যেত এবং কিছু পরবর্তী ঢেউ বা জোয়ারের জল না আসা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারত । এভাবে যে সব মাছ জলে ও স্থলে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করল, তারা হল উভচর প্রাণী । বর্তমানে কুমির, ব্যাঙ এদের বংশধর । এই উভচরদের আবার কতগুলো জলে ফিরে যায় । এদের বংশধর হল তিমি, শুশুক ইত্যাদি । উভচরদের যে দলগুলো স্থায়ীভাবে স্থলে বসবাস শুরু করেছিল, পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের শরীরেও এলো পরিবর্তন । এদের চেপ্টা লেজ আর চেপ্টা রইল না, শল্ক হল পশম এবং পাখনা হল পা । আজ থেকে প্রায় ২৮ কোটি বছর পূর্বে স্থলবাসী উভচর মৎসদের এই দলটি পরিণত হয়েছিল সরীসৃপে ।


মধ্যজীবীয় যুগে গাছপালা, জীবজন্তু বিরাট আকৃতির ছিল । সরীসৃপরাই ছিল সংখ্যায় অধিক এবং বিশালকার । এই যুগটি ছিল মূলত সরীসৃপদের যুগ । ডাইনোসরদের প্রাধান্য ছিল বেশি । এদের কয়েকটি প্রজাতি ছিল । যথা- ব্রন্টোসরাস, ট্রাইরানোসরাস, অল্লোসরাস, গোর্গোসরাস, সেরাটোসরাস, স্টেগোসরাস ইত্যাদি । এদের আকার আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও কিছু বিষয়ের মিল ছিল । এরা পিছনের বড় পা ও লেজের উপর ভর দিয়ে চলাফেরা করত । সামনের ছোট ছোট থাবা দুটি ব্যবহার করত লড়াই ও খাবার শিকারের কাজে । এরা মাংসাশী প্রাণী ।
এই সময়ে সরীসৃপদের একটি দল আকাশে উড়তে শুরু করেছিল । এদের বলা হয় টেরোডাকটিল । এদের গায়ে পালক ছিল না, ডানা ছিল চামড়ার, দাঁত ধারালো, মুখ অনেকটা বাদুড়ের ন্যায় । মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে এরা এত বিশাল হয়েছিল যে, এক ডানার প্রান্ত হতে আর এক ডানার প্রান্তের দৈর্ঘ্য ছিল ২৫ ফুট । এদেরকে বলা হয় আধুনিক পাখির পূর্বপুরুষ । একই যুগেই আবার উড়ন্ত সরীসৃপদের মাঝে রূপান্তর শুরু হয়েছিল । এদের গঠন ছিল পাখি ও সরীসৃপদের মিশ্ররূপ । এ জাতীয় জীবগুলোর নাম আর্কিওপটেরিক্স । এইসব সরীসৃপরা ছিল ডিম্বপ্রসূ জীব । কিন্তু দেখা যায় আজ থেকে প্রায় ১৫ কোটি বছর পূর্বে ট্রিয়াসিক উপযুগে (মধ্যজীবীয় যুগ) একদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী গর্ভধারণ ও বাচ্চা প্রসব করতে শুরু করে । এই সময়টা ছিল স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব কাল । স্তন্যপায়ী জীবেরা প্রকৃতি থেকে দুটি সুবিধা পেয়েছিল । প্রথমত তাদের রক্ত ছিল উষ্ণ, দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে সন্তানবাৎসল্য ছিল, যা অন্য প্রাণীদের ক্ষেতে দেখা যায় না । উষ্ণ রক্তের অধিকারী হওয়ায় স্তন্যপায়ী জীবেরা প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সাথে নিজেদের অধিক খাপ খাওয়াতে পেরেছিল


এয়োসেন উপযুগে (নবজীবীয় যুগ) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বিভিন্ন শাখা ভূপৃষ্টের অধিকাংশ অঞ্চলজুড়ে বসবাস শুরু করেছে । আজ থেকে প্রায় ৭ কোটি বছর পূর্বে এই যুগটি শুরু হয়েছে । বর্তমান যুগের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলানায় সে যুগের স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ছিল আকৃতিতে ছোট । বর্তমান যুগের হাতি, গণ্ডার, ঘোড়া, শূকর ইত্যাদি প্রাণীদের আদিপুরুষ ছিল ফেনাডোকাস নামে একটি স্তন্যপায়ী জীব । এটি আকৃতিতে শেয়ালের চেয়ে বড় ছিল না । স্তন্যপায়ী অন্য একটি শাখার নাম ছিল ক্রিয়োডোন্ট । এরা ছিল হিংস্র ও মাংসাশী প্রাণী । কালের পরিক্রমায় এরা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে । এদের একদলের চেহারা ছিল কুকুরের মত । এই দলের ক্রমবিবর্তনে নেকড়ে বাঘ, ভালুক, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর জন্ম হয়েছে । অন্যদলের চেহারা ছিল বিড়াল আকৃতির । এদের ক্রমবিবর্তনে বাঘ, সিংহ, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছে । স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ছিল । এরা গাছে চড়তে পারত ও ডালে ডালে বিচরণ করত । নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বের সব স্তন্যপায়ী প্রাণী আজ আর বেঁচে নেই । এদের কোন কোন দল বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আবার কোন কোন নতুন দলের আবির্ভাব হয়েছে । এরা বর্তমান পর্যায়ে আসতে ৭ কোটি বছর লেগেছে ।
বনে-জঙ্গলে যে সব প্রাণী মাটিতে চলাফেরা করে তাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তি তীব্র । ঝোপ-জঙ্গলের বাঁধাজনিত কারণে তাদের দৃষ্টিশক্তি তেমন কাজে লাগে না, তাই তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে অধিক কাজে লাগাতে হয়েছিল । কিন্তু যেসব প্রাণী বৃক্ষচারী ছিল তাদের ঘ্রাণশক্তি তেমন কাজে আসেনি । তাদের প্রয়োজন ছিল প্রখর দৃষ্টিশক্তি । এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা, অন্যথায় জীবন বিপন্ন হতে পারে । সুতরাং এই প্রয়োজন ও চর্চা থেকে বৃক্ষচারী জীবদের দৃষ্টিশক্তি উন্নততর হয় এবং চোখ ও অক্ষিগোলকের অবস্থান পরিবর্তিত হয় । অন্যান্য প্রাণীরা দুই চোখে একটি বস্তুর দুটি ছবি দেখে কিন্তু বৃক্ষচারী প্রাণীদের চক্ষুর অবস্থান পরিবর্তন হওয়ার কারণে তারা দেখে একটি । এতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকে । বৃক্ষচারী প্রাণীদের এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে যাওয়ার জন্য সামনের পা দুটিকে ব্যবহার করতে হয় ধরার কাজে । এতে এই পা দুটি হল থাবা । এরা আরও কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল । যেমন বৃক্ষের ডালে ডালে লাফালাফি করতে হলে প্রতি মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হয় । লক্ষ্য স্থির করার জন্য দ্রুত মস্তিষ্ক চালনা করতে করতে ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ক বড় হচ্ছিল । অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার অভ্যাস গড়ে উঠছিল এবং থাবা দুটি ব্যবহার করতে শুরু করল আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজে । দুই পায়ে চলার ফলে এরা কিছু সুবিধা পেয়েছিল । যেমন- আত্মরক্ষার জন্য থাবা দিয়ে লাঠি বা ডালপালা ব্যবহার করা উত্তম এবং মুখ দিয়ে চেটে খাবার খাওয়ার চেয়ে থাবা দিয়ে খাবার গ্রহণের সুবিধা অনেক । এরূপ সুবিধা পেয়ে একদল বৃক্ষচারী জীব দ্বিপদ হয়ে উঠল এবং তাদের থাবা দুটি হাতে পরিণত হল । যেসব চতুষ্পদ জন্তু খাবার গ্রহণের জন্য থাবা ব্যবহার করে না, তাদের মুখমণ্ডল হয় লম্বাটে । যথা- শিয়াল, কুকুর, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি । আর যেসব প্রাণী খাবার গ্রহণের জন্য থাবা ব্যবহার করে তাদের মুখমণ্ডল হয় প্রায় গোলাকৃতির । যথা- বাঘ, সিংহ, বিড়াল ইত্যাদি । দ্বিপদ জন্তুরা খাবার গ্রহণ ও মশা-মাছি তাড়াবার কাজে হাতের ব্যবহার করতে থাকলে তাদের মুখমণ্ডল হতে থাকে গোল এবং লেজের ব্যবহার না হওয়াতে লেজটি হতে থাকে ছোট । কালক্রমে এদের মেরুদন্ডের শেষপ্রান্তে সামান্য একটু নমুনা ছাড়া লেজের আর চিহ্ন থাকল না । এই জাতীয় প্রাণীদের বলা হয় প্যারাপিথেকাস ।

“উক্তরূপে একটি অভিনব জন্তুর উদ্ভব হইলে, কালক্রমে উহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে । উহাদের মধ্যে একটির লেজ নাই, মুখমণ্ডল ঈষৎ গোল, উহারা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে এবং যাবতীয় কাজে হাত ব্যবহার করে । এই জন্তুটি বানর নহে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা বা ওরাংওটাং নহে এবং পুরাপুরি মানুষও নহে । ইংরেজিতে ইহাদিগকে বলা হয় অ্যানথ্রোপয়েড এপ বা মানুষসদৃশ বানর । ইহারাই মানুষের পূর্বপুরুষ । প্যারাপিথেকাসের অপর শাখার জন্তুদের সাথে অ্যানথ্রোপয়েড এপ-এর চালচলন ও আকৃতিগত পার্থক্য সামান্য হইলেও তাহারা বনমানুষের পূর্বপুরুষ ।”
বিবর্তন এমন কোন বিষয় নয় যে এটা হঠাৎ করে ঘটে গেছে । প্রাণীজগতের বর্তমান অবস্থায় আসতে প্রকৃতি সময় নিয়েছে ১৫০ কোটি বছর । বিবর্তনের সবচেয়ে প্রামাণ্য দলিল হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভূগর্ভস্থ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ফসিল । এসব ফসিলগুলোতে দেখা যায় যে ফসিল যত বেশি অতীতের, মানুষের চেহারাও তত বুনো দেখায় । উদ্ধারপ্রাপ্ত ফসিলের সাথে আধুনিক মানুষের অমিলের কারণই হচ্ছে বিবর্তন । ১৯২৪ সালে আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ট্রান্সভাল অঞ্চলে ডিনামাইট দিয়ে একটি মাটির ঢিবি উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল । এই স্থানের মাটি খনন করে আরও নিচে পাওয়া গিয়েছিল ৬ বছর বয়সী একটি বালকের মাথার খুলি । এর গঠন ছিল মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি । খুলিটির বয়স ছিল এক লক্ষ বছরের কিছু বেশি । একে বলা হয় অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ । ১৯৩৬ সালে জোহান্সবার্গের কাছাকাছি স্থানে মাটি খনন করে আর একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথার খুলি ও কিছু হাড়গোড় পাওয়া গিয়েছিল । এটির গঠনও ছিল মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি এবং অস্ট্রালোপিথেকাসের সমবয়সী ও সমগোত্রীয় । একই অঞ্চল হতে ১৯৩৮ সালে একটি মাথার খুলি ও কয়েকটি দাঁত এবং ১৯৪৭ সালে আরও অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল । এগুলো ছিল মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি চেহারার এবং প্রত্যেকের বয়স ছিল এক লক্ষ বছরের কিছু বেশি ।
১৮৯০-৯২ সালে জাভা দ্বীপের পূর্বাংশে মাটি খনন করে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গিয়েছিল মানুষের একটি দাঁত, নিচের চোয়ালের একটি হাড়, উপরের চোয়ালের ডান দিকের একটি পেষণ দাঁত, মাথার খুলি ও ঊরুর একটি হাড় । হল্যান্ডবাসী ইউজেন দুবোয়া নামে একজন ডাক্তার এগুলো উদ্ধার করেছিলেন । বিজ্ঞানীরা এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানিয়েছেন, এগুলো ছিলে অর্ধ বানর ও অর্ধ মানুষের । এসবের বয়স এক লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বছরের মধ্যে । এগুলোকে বলা হয় জাভা মানুষ ।
একজন জার্মান ডাক্তার ১৯০২ সালে পিকিং শহরের নিকটবর্তী স্থান হতে আবিষ্কার করেন একটি দাঁত । ১৯১৬ সালে অন্য একজন জীববিজ্ঞানী ঐ অঞ্চলের মাটি খনন করে উদ্ধার করেন কতগুলো হাড়গোড়, কানাডার একজন জীববিজ্ঞানী ১৯২৭ সালে উদ্ধার করেন একটি দাঁত, একই অঞ্চল হতে একজন চীনা, একজন ফারাসী এবং একজন আমেরিকান জীববিজ্ঞানী খুঁজে পান মাথার খুলি, চোয়ালের হাড় ও দাঁত ইত্যাদি নিদর্শন । চেহারায় ঐ সব পিকিং মানুষগুলো ছিল জাভা মানুষের সমগোত্রীয় ও সমবয়সী ।
১৮৬৫ সালে জার্মানীর নেয়ানডার্থাল নামক স্থানে মাটি খনন করে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাথার খুলি । বিজ্ঞানীদের মতে এই খুলিটি ছিল মানুষের পূর্বপুরুষের । মাটির যে স্তর থেকে এতি আবিষ্কৃত হয়, এর প্রাচীনত্বের হিসাব অনুযায়ী খুলিটির বয়স ছিল ৭৫ হাজার বছর । এটি ছিল নেয়ানডার্থাল মানুষ । ১৯০৮ সালে ফ্রান্সের শাপেন ও-স্যা নামক গ্রামের কাছে একটি গুহা হতে পাওয়া গিয়েছিল একটি আস্ত কঙ্কাল । এটি ছিল একটি মানুষের কঙ্কাল এবং তা নেয়ানডার্থাল মানুষের সমবয়সী ও সমগোত্রীয় । এই কঙ্কালটি হতে মানুষের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া গিয়েছে । এই মানুষটির মুন্ড ছিল প্রকান্ড, ধড় ছোট, ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির মত উচ্চতা । এটি দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু শরীর ও মাথা সামনের দিকে নুয়ে পড়ে এবং হাঁটু বেঁকে যায় । শরীরের তুলনায় মুখ বড় এবং মাথার খুলি চ্যাপ্টা । এটিতে বানরের চেয়ে মানুষের আদলটাই বেশি ।
১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের দোর্দোঞন অঞ্চল থেকে মানুষের ৫টি পূর্ণাবয়ব কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় । এগুলোর উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট ১ ইঞ্চির মধ্যে । এদের মাথা ছিল লম্বা, মুখ থ্যাবড়া, পেশীবহুল প্রত্যঙ্গ ও চোয়াল ছিল উঁচু । চেহারার দিক দিয়ে পুরাপুরি আধুনিক মানুষ । কঙ্কালগুলোর বয়স ছিল মাত্র ৩০ হাজার বছর । এগুলোকে বলা হয় ক্রো-মাঙ্গ মানুষ ।
বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে ১৫০ কোটি বছর পূর্বে । কিন্তু মানুষের আধুনিক রূপ গঠিত হয়েছে মাত্র ৩০ হাজার বছর আগে ।
- আসোয়াদ লদির ব্লগ
আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র- ২
পৃথিবীর ঠিকানা – অমল দাসগুপ্ত

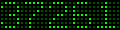




important writing
ReplyDelete