নিয়ানডার্থাল মানবের বিলুপ্তি ও আমাদের দায়ভার"
পৃথিবীতে মানুষের আগমন নিয়ে ধর্ম গ্রন্থের বয়ান আমরা কম বেশী সবাই জানি। ঈশ্বরের কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসেন আদম। ঠিক কবে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তার সঠিক বর্ননা কোথাও নেই। বাইবেলে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আদম পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রায় ছয় হাজার বছর আগে। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী আদম ও ইব্রাহীম নবীর মাঝে বয়সের পার্থক্য উনিশশত আটচল্লিশ বছর। মূসা নবী আবির্ভূত হন যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তেরো শত বছর আগে। সে হিসাবেও আদি পুরুষ আদম প্রায় ছয় হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে মনে করা হয়। অন্য কিছু প্রাচীন তথ্য অনুযায়ী এই সময়টাকে অবশ্য ছয় হাজার বছরের চেয়েও বেশী বলে উল্লেখ করা হলেও কোনক্রমেই তা দশ হাজার বছরের বেশী নয়। পুরাকথা ও ধর্মগ্রন্থে আদম নামের যে আদি পুরুষকে আমরা পাই, তিনি কিন্তু অনেকটা আমাদের মতই আধুনিক মানুষ। নগ্নতায় লজ্জিত, প্রেয়সী ঈভের বিরহে কাতর, ন্যায়ে সন্তুষ্ট, অন্যায়ে সোচ্চার। আদম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন এই ধারণার পিছনে বড় যুক্তি হচ্ছে, অন্যান প্রানীর চেয়ে মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। বানর-শিম্পাঞ্জীকে মানুষের সমগোত্রীয় মনে করা হলেও বুদ্ধিমত্তা ও জীবন যাপনের পার্থক্য এতই প্রকট যে মানব জাতি মর্ত্য জাত নয় বরং স্বর্গ থেকে আগত এমনটি মনে হওয়া স্বাভাবিক।
অন্যদিকে বিজ্ঞান জানাচ্ছে, প্রায় সত্তর লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জী (বনোবো) ও মানুষ বিবর্তনের ধারায় একই সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যায়। আদি মানব হোমো এর আবির্ভাব ঘটে আফ্রিকায়, প্রায় চব্বিশ লক্ষ বছর আগে। সেখান থেকে ক্রমশঃ তারা অন্য মহাদেশ গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।ফসিল গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, আদি মানব হোমোর আবার গোত্র বিভাগ ছিল। ক্রম বিবর্তনে কোন গোত্রের আবির্ভাব ঘটেছে আগে কোনটার পরে। কোন কোন গোত্র আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কেউ টিকে থেকেছে নিকট অতীত পর্যন্ত। এই বিবর্তনের পথে হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষ মানুষের আবির্ভাব ঘটে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে, আফ্রিকায়। ততদিনে আফ্রিকা ও ইউরেশিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে হোমো ইরেক্টাস, ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে হোমো হাইডেলবার্গ, আফ্রিকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে হোমো হাবিলিস গোত্র সমূহ। আমাদের পুর্বপুরুষ স্যাপিয়েন্স মানবের আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করতো একটি ভিন্ন গোত্রের হোমো গোষ্ঠী, যাদের নাম হোমো নিয়ানডার্থালেনসিস (নিয়ানডার্থাল মানব)। জীবাশ্ম-নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায় প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে ঐ অঞ্চলে নিয়ানডার্থাল মানবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মাত্র পচিশ হাজার বছর আগ পর্যন্ত তারা বেঁচে ছিল। নিয়ানডার্থাল মানব বিলুপ্ত হবার পর হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স, অর্থাৎ আমরা ছাড়া হোমো গোত্রের আর কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।
ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটো আলাদা বিষয় হলেও সময়ের অঙ্কে, নিয়ানডার্থাল মানবের বিলুপ্তির প্রায় পনেরো হাজার বছর পরে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ধর্মগ্রন্থ থেকে আদমের আবির্ভাবের কথা জানা যায়। পুরাকালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ত্রিশ বছর। সে হিসেবে নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হবার প্রায় পাঁচশো প্রজন্ম পর, যখন আশেপাশে সমমানের বুদ্ধি সম্পন্ন অন্য কোন কোন প্রাণী নেই, তখন মানুষের মাঝে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্ম নেওয়াটাই স্বাভাবিক যে মানুষ মর্ত্য জাত নয় বরং স্বর্গ থেকে আগত। সে সময়ে মানুষের ভাষা পুর্ণাঙ্গ রূপে বিকশিত হয়নি, ইতিহাস বলতে গোছানো কোন তথ্য ছিল না। যা ছিল, তা হলো পিতা প্রপিতামহের কাছে শোনা গল্প। ফলে পাঁচশো প্রজন্ম পরে রূপকথার নরখাদক রাক্ষস ছাড়া নিয়ানডার্থাল সম্পর্কিত কোন ইতিহাসই উত্তরাধিকার সূত্রে অবশিষ্ট থাকেনি। এখন আমরা নিয়ানডার্থালদের সম্পর্কে যা জানছি তার সবটাই প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও ফসিল গবেষণার ফসল।
নিয়ানডার্থালদের আবির্ভাব ঘটেছিল শেষ তুষার যুগে।ফলে তাদের দৈহিক গঠন ও জীবন যাত্রা ছিল শীতল আবহাওয়ার উপযোগী। নিয়ানডার্থালদের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে এ পর্যন্ত তিনটি প্রস্তাবিত তত্ত্ব রয়েছে। প্রথম তত্ত্ব, প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে শেষ বরফ যুগের অবসান ও আবহাওয়া বিপর্যয় ঘটলে, পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয় তত্ত্বটিকে অনেকে প্রাগৈতিহাসিক ট্রাজেডি বলে অভিহিত করেছেন। হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্সের আধুনিক প্রজন্মকে বলা হয় ক্রো-ম্যাগনন মানুষ, যারা ত্রিশ হাজার বছর আগে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় নতুন করে নিজেদের বসতি বিস্তার লাভে সক্ষম হয়। ধারণা করা হয়,আমাদের প্রত্যক্ষ পূর্ব পুরুষ এই ক্রো-ম্যাগননরা, বসতি বিস্তার ও খাদ্য সংকট মোকাবিলা করার মোক্ষম পন্থা হিসেবে প্রতিদ্বন্দী নিয়ানডার্থালদের মেরে ফেলেছিল। তৃতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, নিয়ানডার্থালরা আদৌ বিলুপ্ত হয়নি বরং অন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে তারা ক্রমাগত মিশে গিয়েছে ক্রো-ম্যাগনন মানুষ অর্থাৎ আমাদের সাথে।
এই তিন তত্ত্বের মধ্য আবহাওয়া বিপর্যয়কে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। নিয়ানডার্থালদের প্রথম ফসিল পাওয়া যায় ১৮৫৬ সালে, জার্মানির নিয়ানডার উপত্যকায়। পরবর্তীতে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলে তাদের অনেক ফসিল আবিষ্কৃত হয়। মুসটিয়ের এলাকায় তাদের ব্যবহৃত পাথুরে অস্ত্রের সন্ধান প্রাপ্তির সূত্রে নিয়ানডার্থাল সংস্কৃতিকে মুসটিয়েরিয়ান সংস্কৃতি বলা হয়। নিয়ানডার্থালরা ছিল শিকারি জাতি। পুরুষের গড় উচ্চতা একশো পয়ষট্টি সেন্টিমিটার, হাড়ের শক্তিশালী গড়নের কারণে ভারী শরীর। দৈহিক দিকে দিয়ে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের চেয়ে শক্তিশালী ছিল তারা, মস্তিষ্কের আয়তন মানুষের চেয়ে সামান্য বেশী থাকায় বুদ্ধির কমতি ছিল না। চোখের কোটরের আকার ছিল বড়, সম্ভবত দৃষ্টি শক্তিও প্রখর ছিল তাদের। মানুষের তুলনায় নাক বড় ছিল, ঠান্ডা বাতাস ফুসফুসে যাবার আগে বড় নাকের ভিতরে উষ্ণায়িত হতো। ঘ্রাণ শক্তিও মানুষের চেয়ে প্রখর ছিল বলে ধারণা করা হয়। বক্ষপিঞ্জর প্রশস্ত, নিতম্ব ও হাত-পায়ের হাড়গুলো ছিল মোটা, তবে দেহের অনুপাতে হাত-পায়ের দৈর্ঘ্য খাটো ছিল। এ ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত শীতল আবহাওয়ায় শরীরে তাপ ধারণ করে টিকে থাকার জন্য উপযোগী। তবে সে জন্য প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার কিলো ক্যালরি পরিমান খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হতো। এই পরিমান ক্যালোরির প্রয়োজনে ম্যামথ, বল্গা হরিণ বা পাহাড়ী ভালুকের মতো বড় প্রাণী শিকার করতো নিয়ানডার্থালরা। শেষ বরফ যুগের অবসানের সাথে সাথে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেলেও নিয়ান্ডার্থালরা তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে পারেনি। অন্যদিকে মানুষের খাদ্যাভাসে বাছবিচার তেমন ছিল না এবং প্রাত্যহিক ক্যালরির প্রয়োজনও ছিল কম। মানুষ লতা পাতা, ফল-মূল, মাছ, শামুক, মাংস সবই খেতে পারতো। ফলে নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে টিকে গিয়েছিল মানুষ।
নিয়েনডার্থালদের বিলুপ্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে নির্বিচার হত্যা যার জন্য দায়ী আমাদের পুর্ব প্রজন্ম, ক্রো-ম্যাগনন মানুষ। নিয়ান্ডার্থালদের তুলনায় ক্রো-ম্যাগননরা কম শক্তিশালী হলেও তাদের গড়ন ছিল অপেক্ষাকৃত হাল্কা যা তাদের দিয়েছিল ক্ষীপ্রতা ও গতি। অস্ত্রগুলো ছিল তুলনামূলক বিচারে উন্নত। খাদ্য তালিকা বহুমূখী হলেও নিয়ান্ডার্থালদের মত স্যাপিয়েন্সরাও ক্রমাগত শিকার নির্ভর হয়ে উঠেছিল। ফলে দুই জাতির মধ্য রক্তক্ষয়ী সংঘাত ছিল অনিবার্য, যার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে ফসিল গবেষণার মাধ্যমে। ১৯৯৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত স্পেনের সিড্রন গুহায় পাওয়া গেছে প্রায় পনেরোশো নিয়ানডার্থাল অস্থি খন্ড। এগুলো ছিলো পাঁচ প্রাপ্ত বয়স্ক, দুই কিশোর, এক বালক ও এক শিশুর। এর মধ্যে খুলির হাড়ে পাওয়া যায় অস্ত্রের আঘাত, যা মানুষের তৈরী অস্ত্রের সাথে মিলে যায়। শুধু আঘাত নয়, কিছু হাড় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এমন ভাবে কাটা হয়েছে যা দেখে বোঝা যায় সেগুলোর সাথে যুক্ত মাংস ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছিলো।
তৃতীয় তও্ব, নিয়ানডার্থাল এবং স্যাপিয়েন্সদের মধ্য অন্তঃপ্রজনন। নিয়ানডার্থাল ও মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য তেমন প্রকট ছিলনা। ১৯৯৫ সালে স্লোভেনিয়ার ডিভেই বাবে গুহায় পাওয়া তেতাল্লিশ হাজার বছর আগেকার একটি বাঁশী যা নিয়ানডার্থালদের তৈরী বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে জার্মানীর হোল ফেলস গুহায় পাওয়া গেছে পয়ত্রিশ হাজার বছর আগে আদি মানুষের তৈরী বাঁশী। এ থেকে বোঝা যায় সে কালে দুই প্রজাতীর মধ্যেই সুরের ধারণা ছিল। দুই জাতিই শিকার করার জন্য নানা ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করতো, জানতো আগুনের ব্যবহার। মৃতদের কবর দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইসরায়েলের কোবারা গুহায় প্রাপ্ত ফসিলের মাধ্যমে জানা গেছে, নিয়ানডার্থালদের গলার অস্থি ও বাগযন্ত্রের গড়ন ছিল অনেকটা মানুষের মতো। নিয়ানডার্থাল ডিএনএ নিয়ে গবেষণায় জানা গেছে, যে জিন এর কারণে মানুষ কথা বলতে পারে, ফক্সপি২ নামক সেই জিনটি তাদেরও রয়েছে। ফসিল ও জেনেটিক গবেষণা যত এগুচ্ছে মানুষ ও নিয়ানডার্থালদের পার্থক্য তত সংকুচিত হয়ে আসছে। সেই প্রেক্ষাপটে, এই দুই গোষ্ঠী দীর্ঘকাল কেবলই মারমারি করেছে একে অপরকে ভালবাসেনি,ভাবাটা কষ্টকর। ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের লাগার ভেলো গুহায় পাওয়া যায় একটি শিশুর ফসিল। প্রাথমিক ভাবে এটিকে চল্লিশ হাজার বছর পূর্বের মানুষ-নিয়ানডার্থাল শংকর শিশু বলে ধারণা করা হয়, যদিও পরবর্তী গবেষনায় তার সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ মেলেনি। এ পর্যন্ত ডি এন এ গবেষণার ফলাফলে, এই দুই প্রজাতির মধ্যে অন্তপ্রজনেনর স্বপক্ষে তেমন জোরালো প্রমাণ মেলেনি। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানর অভিমত, দুটি পৃথক শিকারী-সংগ্রহকারী প্রাণীর সহাবস্থান শান্তিপূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।
নৃবিজ্ঞান গবেষণায় ফসিলের গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিন ধরে এই গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল ফসিলের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, এক্স-রে, আইসোটপ বিশ্লেষণ বা নানা ধরণের স্ক্যানিং পদ্ধতির উপরে। বর্তমানে তার সাথে যুক্ত হয়েছে ডি এন এ বিশ্লেষন, বেরিয়ে আসছে অনেক অজানা তথ্য। এ বিষয়ে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন তাঁদের একজন স্ভ্যান্টে পাবো। ২০১০ সালের জুলাই মাসে বিশ্বখ্যাত সায়েন্স জার্নালে নিয়ানডার্থাল এর জিন বিশ্লেষণের বিষদ ফলাফল প্রকাশ করে পাবো ও তার গবেষক দল। এর মধ্যে নৃবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে দুটি তথ্য। প্রথমত, আফ্রিকার বাইরে অর্থাৎ এশিয়া ও ইউরোপের বর্তমান মানুষদের শতকরা এক থেকে চার ভাগ জিন উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়ানডার্থালদের কাছ থেকে পাওয়া। সময়ের হিসেবে প্রায় আশি হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানবদের সাথে আদি স্যাপিয়েন্স মানুষদের অন্তঃপ্রজননের ফলে এই জিন প্রাপ্তি ঘটেছিল, যে কারণে আফ্রিকার মানুষের মাঝে এই জিন পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয়ত, সেই অন্তঃপ্রজনন ছিল একমুখী, অর্থাৎ মানুষের একাংশের মাঝে নিয়ানডার্থালদের জিন পাওয়া গেলেও নিয়াডার্থালদের মাঝে মানুষের কোন নির্দিষ্ট জিন পাওয়া যায় নি।
নৃবিজ্ঞানীদের চমকে দেওয়া এই জিন বিশ্লেষণ ফলাফলের পটভূমি আর এক বার দেখে নেওয়া যাক।এক লক্ষ বছর আগে আমাদের আদি পুরুষ, অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স মানবদের একটি অংশ আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে পাড়ি জমায়।সে সময় মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে বাস করতো নিয়াডার্থাল মানবেরা। শান্তিপূর্ণ না হলেও স্যাপিয়েন্স ও নিয়াডার্থালদের সহাবস্থান কাল ছিল প্রায় পঁচাত্তর হাজার বছর। তার পর স্যাপিয়েন্সরা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম ক্রো-ম্যাগনন মানুষে রূপান্তরিত হয়। সেই রূপান্তরের পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে নিয়াডার্থালদের। তথ্যগুলোয় ফাঁক রয়েছে, রয়েছে অনেকগুলো জলন্ত প্রশ্ন। প্রায় আশি হাজার বছর আগে নিয়ান্ডার্থালদের সাথে মানুষের অন্তঃপ্রজনন এক মুখী ছিল কেন? ফসিল রেকর্ডে স্যাপিয়েন্স-নিয়াডার্থাল শংকর প্রজাতি অনুপস্থিত কেন? লক্ষ বছরের পরিক্রমায় নিয়ান্ডার্থালদের বিবর্তন প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়নি, তাহলে স্যাপিয়েন্সরা ক্রো-ম্যাগনন মানুষে রূপান্তরিত হলো কেন? জীবাশ্ম-নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এখন পর্যন্ত এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, তবে এ সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে প্রস্তাবিত একটি তত্ত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বোদ্ধাদের।

তত্ত্ব প্রস্তাবকের নাম ড্যানি ভেন্ড্রামিনি।অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ভেন্ড্রামিনি প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী নন, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীও নেই তার। তবে নৃবিজ্ঞানে স্ব-শিক্ষিত তিনি এবং এ বিষয়ে প্রবন্ধ, বইও লিখেছেন। বইয়ের নাম, দেম প্লাস আস (তারা যোগ আমরা)। নানা তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছেন, নিয়ানডার্থাল প্রেডেটর তত্ত্ব।তার তত্ত্ব অনুযায়ী নিয়ানডার্থালরা ছিল শিকারজীবি এবং তাদের জীবন যাত্রার সঙ্গে মিল ছিল বাঘ-সিংহ জাতীয় মাংসাশী শিকারী প্রাণীর। এসব প্রাণী অন্যান্য প্রাণীদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করার সাথে সাথে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক আচরণ প্রদর্শন করে।দীর্ঘ পচাত্তর হাজার বছর যাবত আদি মানুষের সাথে নিয়ানডার্থালদের আচরণ ছিল এরকম হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক।
আদি মানুষের মাঝে শ্রমের শ্রেনিবিভাগ ছিল, যেমন শিশু ও মেয়েরা গুহায় থাকতো, শিকারে যেত পুরুষেরা। নিয়ানডার্থালদের এ রকম শ্রেণীবিভাগ ছিলনা। শিশু, মেয়ে, পুরুষ সবাই একসাথে শিকার করত, ফলে তাদের ভিতরে শিকারী প্রবৃত্তি ছিল প্রায় জন্মগত। প্রকৃতিতে শিকারী নিয়ানডার্থালদের অবস্থান ছিল ফুড চেইনের শীর্ষে, মানুষের অবস্থান তাদের নীচে। মানুষের চেয়ে দৈহিক দিকে দিয়ে অধিক শক্তিশালী, প্রখর দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন নিয়ানডার্থালরা নিজেদের বিবেচনা করতো খাদক এবং বাকী সব প্রাণী এমনকি মানুষকে মনে করতো তাদের খাবার। ভেন্ড্রামিনির মতে, প্রায় এক লক্ষ বছর আগে আদি মানুষ আফ্রিকা থেকে মধ্য এশিয়া-ইউরোপে এলে নিয়ানডার্থালদের হিংস্র আক্রমণের শিকার হয়। অনেককে মেরে, ক্ষেত্র বিশেষে খেয়ে ফেলা হয়। ভেন্ড্রামিনি ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স ও স্পেনের একাধিক ফসিল সাইটের উল্লেখ করেছেন যেখানে নিয়ানডার্থালরা যে নরখাদক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্রোয়েশিয়ার ভিন্ডিযা গুহা সহ অন্যান্য গুহায় প্রাপ্ত নিয়ানডার্থালদের হাড়ের কার্বন ও নাইট্রোজেন আইসোটোপ বিশ্লেষণ করে জানা গেছে তাদের খাদ্যে শব্জির পরিমান ছিল প্রায় শূন্য। সে তূলনায় মানুষের খাদ্যের অর্ধেকটা ছিল উদ্ভিদ জাত।
মানুষকে আক্রমণ করার একটি বাড়তি কারণও ছিল নিয়ানডার্থালদের। তা হলো যৌন লিপ্সা। মানুষ ও নিয়ানডার্থেলদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কাঠামোগত কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ই আদি হোমো গোত্রীয় হওয়ায়, মৌলিক মিল ছিল। শক্তিশালী নিয়ানডার্থাল পুরূষের কাছে দুর্বল মানব নারী ছিল লোভনীয় যৌন শিকার। নিয়ানডার্থাল নারীরা ছিল শিকারী এবং স্বাভাবিক ভাবেই শক্তিশালী। ফলে পুরুষের যৌন চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে তাদের উপরে জোর জবরদস্তি খুব একটা কার্যকর হবার কথা নয়। অন্য দিকে অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র ও দুর্বল মানব নারীদের উপরে বলাৎকার করা সহজতর ছিল। প্রাণী জগতে মেয়েদের ডিম্বক্ষরনের সাথে হরমোন ও ফেরোমনের নিঃসরণ সম্পৃক্ত। এই ফেরোমেনের গন্ধ অনেক পুরুষ প্রাণীর নাকে মেয়েদের ডিম্ব ক্ষরন ও যৌন মিলনের সংকেত পৌঁছে দেয়, পুরুষদের মিলনোন্মুখ করে তোলে। প্রখর দৃষ্টি ও ঘ্রাণ শক্তি সম্পন্ন নিয়ানডার্থালরা অনেক দূর থেকেও মানুষের উপস্থিতি টের পেতো। সেই সাথে টের পেতো মেয়েদের ডিম্বক্ষরনের সময়ে নিসৃত ফেরোমনের গন্ধ, যা তাদের জৈবিক কারণেই উত্তেজিত করে তুলতো।
ভেন্ড্রামিনির তত্ত্ব অনুযায়ী, এক লক্ষ বছর আগে উত্তর আফ্রিকায় মরুকরণ শুরু হলে সেখানকার অনেক মানুষ প্রথমে লেভান্ট অঞ্চলে দেশান্তরিত হয়। লেভান্ট হচ্ছে আফ্রিকা ও ইউরোপকে সংযুক্তকারি মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চল, বর্তমানে যেখানে জর্ডান, ইসরাইল, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, তুরষ্ক রাষ্ট্রসমূহ অবস্থিত। এই অঞ্চল থেকে তুরষ্ক পেরিয়ে কৃষ্ণ সাগরের পুর্ব ও পশ্চিম পাড় ধরে আদি মানুষ সে সময়ে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া ঢুকেছিল। তবে নিয়ানডার্থালদের ক্রমাগত আক্রমণে হারিয়ে যেতে থাকে তারা। এমনকি লেভান্ট অঞ্চলেও মানব জনসংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়।ভেন্ড্রামিনি একে বলেছেন জনসংখ্যার “বটল নেক” (বোতলের সরু গলা) ক্রান্তি কাল। ফসিল গবেষকদের তথ্য অনু্যায়ী আশি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়ে সবচেয়ে কম সংখ্যক মানব ফসিল পাওয়া গেছে লেভান্ট অঞ্চলে, যদিও একই সময়ে সেখানে পাওয়া গেছে নিয়ানডার্থালদের অনেক ফসিল। আগে আদি মানুষ ব্যবহার করতো পরে নিয়ানডার্থালরা ব্যবহার করেছে, এমন একাধিক গুহার সন্ধানও পাওয়া গেছে এ অঞ্চলে।
ফুড চেইন এ শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখতে শিকারী নিয়ানডার্থালরা নির্ভর করেছিলে দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্যের উপর।অপরদিকে তাদের শিকার না হবার জন্য কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের। উত্তর আফ্রিকা তখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে ফেরার জায়গা নেই, কৌশলে টিকে না থাকতে পারলে মৃত্যু অবধারিত। ফলে, টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিই প্রাকৃতিক ভাবে ক্রমাগত নির্বাচিত হতে থাকে মানুষের জেনেটিক কোড এ। ক্রো-ম্যাগনন মানব সেই ক্রমাগত রূপান্তরের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ।
ভেন্ড্রামিনির মতে, ক্রো-ম্যাগনন মানুষের অধিকাংশ শারীরিক ও সামাজিক পরিবর্তনই ঘটেছিল শিকারী নিয়ানডার্থালদের প্রতিরোধকল্পে। ক্রো-ম্যাগননদের হাত পায়ের হাড় নিয়ানডার্থালদের তুলনায় হালকা হলেও তাদের পেশী ছিল দ্রুত দেহ সঞ্চালনের উপযোগী, যেমন দ্রুত আঘাত করা বা দ্রুত দৌঁড়ে পালানো। নিয়ানডার্থালরা মূলত হাতে ধরা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে শিকারে অভ্যস্ত হলেও ক্রো-ম্যাগননরা বর্শা জাতীয় ছুঁড়ে মারার অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। আদি স্যাপিয়েন্স মানুষ মূলতঃ খাদ্য আহরণকারী হলেও ক্রো-ম্যাগননরা কালক্রমে শিকারে দক্ষত অর্জন করে। আক্রান্ত হলে পালিয়ে আত্মরক্ষা নয়,পাল্টা আক্রমণ করতে শেখে তারা। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিততে বড় জোট তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আদি মানুষ বিশ পচিশ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার ভিত্তিক দলে বিভক্ত হলেও ক্রো-ম্যাগননদের ভিতরে সংস্কৃতি চর্চা যেমন সঙ্গীত এবং ধর্মীয় প্রথার প্রচলন শুরু হয়।এর ফলে পরিবারের বাইরে একই সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় পরিমন্ডলের মানুষকে স্বদলীয় ভাবা সহজতর হয়ে ওঠে এবং বড় দল গঠন করা সম্ভবপর হয়। নিয়ানডার্থালদের বিরুদ্ধে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের আত্মরক্ষা বা আক্রমণ উভয়ই হয়ে ওঠে অধিক সম্মিলিত ও কৌশলী। তীব্র দৃষ্টি ও ঘ্রাণ শক্তির সাথে পাল্লা দিতে বুনো কুকুর বা নেকড়ে জাতীয় প্রাণীকে পোষ মানিয়ে ব্যবহার করা শুরু হয়।
পোষাক পরার প্রচলন চালু হয়। এর ফলে এক দিকে যেমন তীব্রে শীতে কম ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করে টিকে থাকা সহজতর হয়, অন্যদিকে তা ক্যামোফ্লেজ হিসেবে কাজ করে। পোষাক অর্থাৎ অন্য প্রাণীর চামড়া বা লতাপাতায় শরীর ঢাকার ফলে মেয়েদের শরীর থেকে নিঃসৃত ফেরোমনের গন্ধ লুকোনো সহজতর হয়। সেই সাথে শরীর ধোয়ার (স্নান) অভ্যাসও গড়ে ওঠে। এর ফলে গায়ের লোম কমে যেতে থাকে চমড়া হতে থাকে মসৃন। যৌন মিলন ও প্রজননের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জী বা বনোবোদের ভিতরে বহুগামিতা পরিলক্ষিত হয়। আদি মানুষ বা নিয়ানডার্থালরাও ছিল বহুগামী। তবে মানব নারীদের দ্বারা প্ররোচিত নিয়ানডার্থালদের আক্রমণ এড়াতে ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মাঝে একগামিতা গড়ে ওঠে। একজন নারী কেবল একজন পুরুষের সাথে যৌন মিলন ও প্রজনন ঘটাবে এই নিয়ম নারীদের জন্য অহেতুক আত্মপ্রদর্শনের অন্তরায় হয়ে ওঠে।আক্রান্ত হলে নির্দিষ্ট পুরুষ তাকে রক্ষা করবে, গড়ে ওঠে সেই নিয়ম। পারিবারিক উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত হয় যার সাথে যুক্ত হয় শিশু হত্যা। অনাকাংখিত শিশু, বিশেষ করে নিয়ানডার্থাল-মানব শংকর শিশু জন্মালে তা হত্যা করা হয়। অাএত সব দৈহিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে ক্রো-ম্যাগননরা বিজয়ী হতে শুরু করে নিয়ানডার্থালের সাথে প্রতিযোগিতায়। পুনর্বার ইউরোপ এশিয়া সহ সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে তারা।
অপর দিকে নিয়ানডার্থালদের যে নিজস্ব সমাজ কাঠামো, সংস্কৃতি বা ধর্ম ছিল না তা কিন্তু নয়। তবে দীর্ঘকাল ফুড চেইনের শীর্ষে অবস্থান করার কারণে, বদলে যাবার বা বিরূপ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার চাপ কম ছিল। শেষের দিকে চাপে পড়ে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা তারাও করেছিল। জিব্রাল্টারের গোরহাম গুহা ও ভ্যানগার্ড গুহায় প্রাপ্ত ফসিল থেকে জানা গেছে চব্বিশ হাজার বছর আগে কেবল ম্যামথ বা বিশাল স্থলচারী প্রাণী নয়, ডলফিন ও সিল মাছ শিকার করতো নিয়ানডার্থালরা, ঝিনুক কুড়াতো সমুদ্রের তীরে। তবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সেই চেষ্টা বোধ হয় বেশী দেরীতে হয়েছিল কারণ ততদিনে ক্রো-ম্যাগননরা দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছে মধ্য এশিয়া ও ইউরোপে।
ভেন্ড্রামিনি তত্ত্ব এখনো জীবাশ্ম-নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের দ্বারা সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত নয়। তবে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত হওয়ার কারণে কেউ তা অস্বীকারও করতে পারছে না। “আশি হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থালদের সাথে মানুষের একমুখী অন্তঃপ্রজনন ঘটেছিল” নৃবিজ্ঞানী পাবো ও তার দলের সদ্য প্রকাশিত ডিএনএ বিশ্লেষনের ফলাফল ভেন্ড্রামিনি তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ন। সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়,অতি আগ্রাসী জীবনই নিয়ানডার্থালদের বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের স্থান দখল করে নিয়েছিল ক্রো-ম্যাগনন মানুষ। তার পর ত্রিশ হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও সেই ক্রো-ম্যাগননদের উত্তরাধিকারী আধুনিক মানুষের আগ্রাসন কিন্তু এখনও কমেনি। যার ফলে আজ হারিয়ে গেছে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সহ পৃথিবীর অনেক আদি সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই আগ্রাসন যদি অব্যহত থাকে তা হলে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে গোটা মানুষ জাতিই যে নিয়ানডার্থালদের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, এমন গ্যারান্টি কিন্তু নেই।
কৃতজ্ঞতা- ⟱
( শেখ আলীমুজ্জামান ভাইয়ের প্রতি)


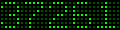




No comments